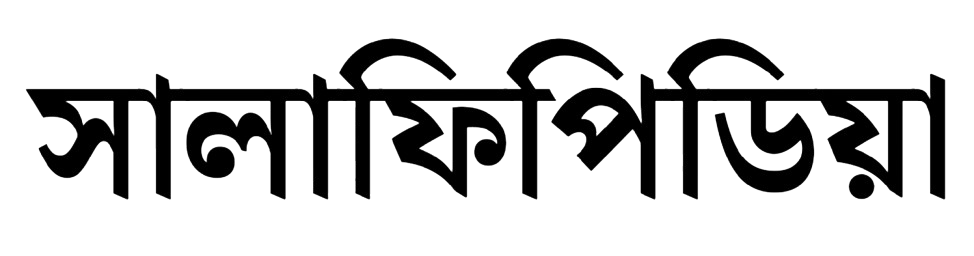আরবি লিপিতে বাংলা লিখন
ফার্সি-আরবি লিপিতে (শাহমুখী লিপি) বাংলা লিখন[১][২] বা হুরুফুল কুরআনে বাংলা[৩] বলতে ফার্সি-আরবি বর্ণমালায় (শাহমুখী লিপি) বাংলা ভাষা লেখালেখি এবং/অথবা বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত দেশি-তৎসম (দ্রাবিড়-সংস্কৃত) ও অমুসলিম বিশ্বে ব্যবহৃত বিদেশি শব্দের পরিবর্তে মুসলিম বিশ্বে ব্যবহৃত আরবি-ফারসি-তুর্কি শব্দসমূহের অধিক ব্যবহারকে বোঝায়। নবাবি আমলে বাংলায় এই পদ্ধতিতে লিখন প্রচলিত ছিল, যাকে পরবর্তীতে ভাষাবিদগণ দোভাষী নামে নামকরণ করেন। পাকিস্তান গঠনের পর পূর্ব বাংলায় এই লিখন পদ্ধতিটি আবার রাজনৈতিকভাবে আলোচনায় আসে,[৪][৫][৬] তখন এই ভাষাকে পাকিস্তানি বাংলা ভাষা[৭][৮] বা পাক-বাংলা ভাষা[৩][৯] হিসেবে অভিহিত করা হয়েছিলো।
ইতিহাস[সম্পাদনা | উৎস সম্পাদনা]
নবাবী বাংলায়[সম্পাদনা | উৎস সম্পাদনা]
টেমপ্লেট:মূল বাংলার নবাবি যুগে, মুসলিম পুথি লেখকদের মধ্যে লেখার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, প্রায় সমস্ত মুসলিম বাঙালি পুথি লেখকরা কিছু হিন্দু লেখক সহ এই লেখালেখির পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন, যাদেরকে ১৮১৮ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বর্তমানে প্রচলিত বাংলা বর্ণমালা বিন্যাস করার সময় এই লেখনরীতিকে দোভাষী পুথি বা বটতলার পুথি নামে নামকরণ করেন।[১০] এবং ৭২টি পুথি তৎকালীন শৈলী অনুসরণ করে লেখা পাওয়া গেছে, যার মধ্যে আছে আলাওলের পদ্মাবতী,[১১], শাহ মুহাম্মদ সগীর এর ইউসুফ-জুলেখা[১২], মুহাম্মাদ আলী কর্তৃক হাইরাত আল-ফিকহ[১৩], মুহাম্মদ ফাসিহ[১৪] ইত্যাদি। এর মধ্যে কিছু নমুনা বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর-এর গ্যালারি-৩৩ (পান্ডুলিপি ও নথিপত্র) এও সংরক্ষিত আছে যার মধ্যে আছে শেখ মুত্তালিবের কেফায়াতুল মুসাল্লিন[১৫] (১৫৫৯) এবং মুহাম্মদ খানের "মাকতুল হুসাইন" (১৬৪৫)।[১৬] এরকম দোভাষী পুথি বিভিন্ন আর্কাইভ ভবনে, ঢাবির পাঠাগারে, বরেন্দ্র জাদুঘরে কয়েক হাজার আছে। শেখ মুত্তালিব তাঁর কেফায়াত আল-মুসাল্লিন গ্রন্থের মুখবন্ধে এই বক্তব্যটি দিয়েছেন: আমি এই সত্য সম্পর্কে অবগত যে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে বাংলায় লিখতে গিয়ে আমি সীমাহীন পাপ করছি।[১৭][১৮]
১৯৪৭-এর পর নব্য পাকিস্তান শাসনামলে[সম্পাদনা | উৎস সম্পাদনা]
টেমপ্লেট:আরও দেখুন পাকিস্তান গঠনের পর থেকেই নব্য পাকিস্তানে বাংলা ভাষায় আরবি হরফ প্রবর্তনের পক্ষে একদিকে ধর্মীয় আবেগ, অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় সংহতির যুক্তি ছিল।[১৯] বলা হচ্ছিল, উর্দু ছাড়া পশতু, সিন্ধি, পাঞ্জাবি ভাষায় আরবি হরফ যেহেতু ব্যবহৃত হচ্ছে—এখন বাংলায় এই হরফের প্রবর্তন করলে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ও সাংস্কৃতিক সংহতি দৃঢ় হবে। এছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার কমিয়ে তার পরিবর্তে আরবি ফারসি উর্দু ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হয়।[২০] এর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা সচিব বা শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান।[২১] এ বিষয়ে তিনি পূর্ব বাংলার শিক্ষাবিদদের সহযোগিতা নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। ১৯৪৮ সালে করাচিতে নিখিল পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলনে শিক্ষা সচিবের এ প্রস্তাব করেন। ১৯৪৯ সালের পেশোয়ারে কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের সভায়ও আরবিকে পাকিস্তানের ভাষা সমূহের একমাত্র হরফ করার জোর সুপারিশ করা হয়।[২২] ফজলুর রহমান ১৯৪৯ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি পেশোয়ারে পাকিস্তান শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের দ্বিতীয় অধিবেশনে দেওয়া বক্তৃতায় বলেন, একই জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠার পথে যেসব অসুবিধা আছে তার মধ্যে নানারকম হরফের সমস্যাটি অন্যতম। এ প্রসঙ্গে তিনি আরবি বর্ণমালার উপযোগিতার কথা বর্ণনা করেন। এ ভাষাকে অনেক একাডেমিক ব্যক্তিত্ব পাকবাংলা ভাষা ও সেসময়ের মুসলিম বাংলা সাহিত্যকে পাকবাংলা সাহিত্য নামে উল্লেখ করেছেন। যখন ফজলুর রহমান ভাষার ইসলামিকরণের স্বার্থে বাংলাকে আরবি লিপিতে লেখার প্রস্তাব করেছিলেন, মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ জটিলতা বৃদ্ধির আশঙ্কা করে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন, এবং বাংলাকে অপরিবর্তিত অবস্থায় পূর্ব বাংলা রাষ্ট্রভাষা তথা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে মত দিয়েছিলেন।[২৩] মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ বিশ্বাস করতেন যে, বাঙালিরা ইংরেজি শেখার সাথে সাথে উর্দু শিখতে পারে, তিনি এও বিশ্বাস করতেন যে: "যেদিন আরবি পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে, সেদিন পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি ন্যায়সঙ্গত হবে।"[২৪][২৫][২৬] ১৯৪৮ সালের মার্চের ভাষা আন্দোলন স্তিমিত হয়ে এলেও পাকিস্তান সরকারের আরবি হরফ প্রচলনের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিক্রিয়া ও প্রতিরোধ অব্যাহত থাকে। ১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থীরা এক সভায় আরবি হরফ প্রচলনের চেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। এতে সভাপতিত্ব করেন মুস্তাফা নূরউল ইসলাম। এ সভায় বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থীদের নিয়ে একটি সংসদ গঠন করা হয়। মো. নুরুল ইসলাম সভাপতি এবং ইলা দাশগুপ্তা ও আশরাফ সিদ্দিকী যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক নির্বাচত হন। এছাড়া নজরুল ইসলাম, মমতাজ বেগম, রিজিয়া খাতুন, খলিলুর রহমানসহ অন্যদের নিয়ে বর্ণমালা সাব-কমিটি গঠিত হয়। এদিকে, ১৯৪৯ সালের ১২ মার্চ বাজেট অধিবেশনের ২য় দিনে ছাত্র ফেডারেশনের একটি বিক্ষোভ মিছিল পরিষদ ভবনের সামনে যাওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ বাধা দেয় এবং আফজল হোসেন, মৃণালকান্তি বাড়রী, বাহাউদ্দীন চৌধুরী, ইকবাল আনসারী খান, আবদুস সালাম ও এ কে এম মনিরুজ্জামান চৌধুরীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এদের জামিন না দিয়ে বন্দি রাখা হয়। ১৯৪৯ সালের এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের ভাষা কমিটির পক্ষ থেকে নঈমুদ্দিন আহমদ সংবাদপত্রে এক বিবৃতিতে বলেন, "পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষিত লোকের হার শতকরা ১২ থেকে ১৫ জন। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের শিক্ষিত লোকের হার শতকরা পাঁচ জনের কম; আরবি বর্ণমালার দোহাই দিয়ে এই ১৫ জন শিক্ষিতকে কলমের এক খোঁচায় অশিক্ষিতে পরিণত করার চেষ্টা চলছে। এর ফলে গোটা পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থাই বানচাল হয়ে যাবে।"[২৭] ১৯৫০ এর শতকে পূর্ব বাংলা সরকারের পক্ষ থেকে ভাষা সমস্যার ব্যাপারে একটি বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানতে মাওলানা আকরাম খানের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটি গঠন করা হয় এবং এ বিষয়টি নিয়ে একটি প্রতিবেদন তৈরি করতে বলা হয়। প্রকল্পের অংশ হিসেবে তারা ১৯৫০ সালে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জেলায় আরবি হরফে বাংলা শিক্ষার ২০টি কেন্দ্র স্থাপন করে।[২৮] ১৯৫০ সালের ৬ ডিসেম্বরের মধ্যে কমিটি তাদের প্রতিবেদন তৈরি করে। তবে এটি ১৯৫৮ সালের আগে প্রকাশ করা হয়নি। এখানে ভাষা সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে সরকারের পক্ষ থেকে একটি কার্যকর ব্যবস্থার প্রস্তাব করা হয়। যেখানে তারা বাংলাকে আরবি হরফে মাধ্যমে লেখার সুপারিশ করেছিলেন।[২৯] পূর্ব বাংলার ভাষা সংস্কার কমিটির সদস্য মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ এই নীতির নিন্দায় ছাত্রদের সাথে যোগ দেন।[১৯] ১৯৫০ সালে গণপরিষদে আরবি হরফে বাংলা লেখার প্রস্তাব উপস্থাপিত হলে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রতিবাদ করে বাংলা ভাষাকে পাক-পরিষদের অন্যান্য ভাষার সহিত সমানাধিকার দানের প্রস্তাব উত্থাপন করেন।[৩০]
পাকিস্তান সরকার ১৯৫১ সালের ২৭শে মার্চ সিএপি-তে আরবি হরফে বাংলা লেখার প্রস্তাব পুনঃপ্রবর্তন করে বাংলার জন্য আরবি লিপির প্রতিস্থাপনের জন্য চাপ দেয়। পূর্ব বাংলার আরও অল্প কয়েকজন বিধায়কের মধ্যে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলাকে পরিবর্তন করার পরিকল্পনার তীব্র সমালোচনা করে বলেন যে, বাংলা লেখার জন্য বিদেশী লিপি প্রবর্তন করে পূর্ব বাংলার মানুষকে নিকৃষ্ট শ্রেণীর নিরক্ষর নাগরিকে পরিণত করা হচ্ছে। তিনি বাংলা বর্ণমালার জন্য আরবি লিপি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেন। যখন বাংলা লেখার জন্য আরবি লিপি গ্রহণের একই প্রস্তাবটি ১৯৫০ সালের এপ্রিলে পাকিস্তানের গণপরিষদে (CAP) আনুষ্ঠানিকভাবে আলোচনা করা হয়, তখন তিনি জোর দিয়ে বাংলার পক্ষে কথা বলেন। বিশেষ করে, তিনি বাংলা বর্ণমালার পরিবর্তে আরবি লিপি প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত সরাসরি প্রত্যাখ্যানের দাবি জানান এবং অবিলম্বে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত সিএপি ফ্লোরে জোর দিয়ে বলেন: "আমি কেবল হিন্দুদেরই নয়, মুসলমানদেরও প্রতিনিধিত্ব করি। আমি আপনাকে বলতে পারি যে পূর্ব বাংলায় যে ভাষা (অর্থাৎ আরবি) চালু করতে চাওয়া হয়েছে তা সাধারণ মানুষ বুঝতে পারবে না। সেই নীতি হবে বদলাতে হবে। আমি জানি না সরকার এই সত্যটি সম্পর্কে অবগত কিনা যে জনগণের বিশাল অংশের মধ্যে এবং বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সম্মেলনে বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি উঠেছে।"[৩১]
১৯৫৩ সালের ৩০ এপ্রিল দত্ত সংসদ অধিবেশনের অর্থবিলের আলোচনাকালে এর সমালোচনা করে বলেন, "তারপর স্যার, আরেকটি বিষয় আছে যা আমি উল্লেখ করব। আমি সংক্ষেপে বলতে চাই কারণ মাননীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ‘জান্নাত’ সিনেমা দিয়ে আমাদের বিনোদন দিয়েছেন এবং আমাকে বেশি সমালোচনা না করতে বলেছেন! আমি অবশ্যই তার ইচ্ছাকে সম্মান করব, তবে আরেকটি বিষয় যা উল্লেখ করা হয়েছে তা হল আরবি লিপির মাধ্যমে বাংলা শেখানো। মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী, যিনি কিছুকাল আগে শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন, তিনি এই হাউসকে বলেছিলেন যে এটি পূর্ববঙ্গে খুব জনপ্রিয় কিন্তু তা নয়। যদি আমরা বিষয়টি অনুসন্ধান করি তবে দেখা যাবে যে এটি সত্যিই অত্যন্ত অজনপ্রিয় এবং পূর্ব বাংলার কেউই চায় না যে বাংলা লিপি বিলুপ্ত করা হোক এবং বাংলা শিক্ষা আরবি লিপিতে করা হোক, কিন্তু স্যার, সরকার এই বিষয়টিকে অনুসরণ করতে চায় এবং স্যার, এটি সরকারের অগণতান্ত্রিক চেতনাকে প্রদর্শন করে।"।[৩২]
১৯৫৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সুলাইমান নদভীকে একটি সেমিনারে আনা হয়েছিল, সেখানে তিনি এই ভাষারীতির পক্ষে কথা বলেন। ভাষণ শেষে বের হওয়ার সময় ছাত্ররা তাকে মারধর করে। সেসময় মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, সৈয়দ আলী আহসান প্রমুখগণ ছাত্রদের রোষ থেকে তাকে রক্ষা করেন।
সমালোচনা[সম্পাদনা | উৎস সম্পাদনা]
সায়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী বলেন, বাংলা ভাষার লিখন পদ্ধতিকে আরবি হরফ থেকে সরিয়ে সংস্কৃত অক্ষরে নিয়ে যাওয়ার এই সিদ্ধান্তটি ছিল এ অঞ্চলের মুসলিমদের ধর্মীয় সত্ত্বার জন্য চরম আত্মঘাতি। এই এক সিদ্ধান্তের ফলে এতদাঞ্চলের বিশাল এক জনগোষ্ঠী আরবি হরফে লেখা ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের সুবিশাল জ্ঞান-ভাণ্ডার থেকে 'আজনবি' হয়ে যায়। তার মতে, তুর্কি ভাষা নিয়েও একই ধরনের পরিকল্পনা হয়েছিল। তিনি বলেন, হাজার বছর পর্যন্ত যে তুর্কি ভাষা আরবি হরফে লেখা হত, কামালবাদের কারণে সেই ভাষার লিখনশৈলি আরবি হরফ থেকে সরিয়ে রোমান/ইংরেজি হরফে নেয়ার ফলে সেখানকার বিশাল মুসলিম জনগোষ্ঠীকে তাদের হাজার বছরের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস-ঐতিহ্য থেকে, হাজার বছরের ইসলামি জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে অপরিচিত বানিয়ে দেয়া হয়েছে।
জিয়ার শাসনামলে[সম্পাদনা | উৎস সম্পাদনা]
শেখ মুজিবকে হত্যার পর জিয়াউর রহমানের শাসনামলে, তার কিছু আধিপত্যবাদী পদক্ষেপ গ্রহণের দিকে প্রতিবেশী বাংলার সাথে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক থেকে মুক্ত একটি 'জাতীয় ব্যক্তিত্বের' আহ্বান জানানোর উদ্বেগের দ্বারা পরিচালিত করা হয়েছিল। বাংলাদেশের ভাষা, ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য, বিশেষ করে ভাষার ক্ষেত্রে, বাংলা ভাষাকে ফারসি ও আরবি শব্দভান্ডারের শব্দ দিয়ে দো-ভাষা (দ্বি-ভাষা) পুনরুজ্জীবিত করার ব্যবস্থা বা কৃত্রিম ব্যবস্থা তৈরি করার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল, যাকে দেশভাগ-পরবর্তী সময়ের "পাক-বাংলা" ভাষা হিসেবে আবুল মনসুর আহমেদ বর্ণনা করেছেন।[৩৩] এইভাবে, 'জয় বাংলা'-- ভাষাতাত্ত্বিকভাবে পূর্ব বাংলার উৎপত্তিগত স্লোগানটি আরও ফার্সিকৃত রুপান্তর "বাংলাদেশ জিন্দাবাদ" দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়েছিল।[৩৪]
নমুনা[সম্পাদনা | উৎস সম্পাদনা]
বাংলা লিপিতে[সম্পাদনা | উৎস সম্পাদনা]
ধারা ১: সমস্ত মানুষ স্বাধীনভাবে সমান মর্যাদা এবং অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। তাঁদের বিবেক এবং বুদ্ধি আছে; সুতরাং সকলেরই একে অপরের প্রতি ভ্রাতৃত্বসুলভ মনোভাব নিয়ে আচরণ করা উচিত।
শাহমুখী লিপিতে[সম্পাদনা | উৎস সম্পাদনা]
دھارا ۱: سمسْت مانُش سْبادھین بھابے سمان مرْیادا اےبں ادھِکار نِیے جنْم گْرہݨ کرے۔ تاںدیر بِبےک اےبں بُدّھِ آچھے؛ سُتراں سکلیرئ اےکے اپریر پْرتِ بھْراتِْرتْب سُلبھ منوبھاب نیے آچرݨ کرا اُچِت۔
ইংরেজি প্রতিবর্ণীকরণ[সম্পাদনা | উৎস সম্পাদনা]
এখানে সুভাষ ভট্টাচার্যের ইংরেজি প্রতিবর্ণীকরণ (আধ্বব চিহ্ন) ব্যবহার করা হয়েছে।[৩৫]
/ d̪ʱara æk | ʃɔmost̪o manuʃ ʃa̪d̪ʱinbʱabe ʃoman mɔrɟad̪a ebɔŋ od̪ʱikar nie̯ ɟɔnmoɡroɦon kɔre | t̪ãd̪er bibek ebɔŋ budʱːi acʰe | ʃut̪oraŋ ʃɔkoleri æke ɔporer prot̪i bʱat̪rit̪ːoʃulɔbʱ monobʱab nie̯ acoron kɔra ucit̪ /
আরবি, উর্দু ও ফারসি শব্দের আধিক্যযুক্ত বাংলা ভাষা[সম্পাদনা | উৎস সম্পাদনা]
বাংলা লিপিতে[সম্পাদনা | উৎস সম্পাদনা]
দফা ১: তামাম ইনসান/মর্দ আজাদভাবে বরাবর ওকার/কারামাত/ইহতিরাম/তাউজু/ইনতিবাহ আর হক লয়ে পয়দা হয়। তাদের দমীর ও আকল আছে; তো সবারই একে অপরের মোতাবেক বেরাদরি/ইখওয়ানি আখলাকের সাথে রোয়া/সুলুক করা চাই।
শাহমুখী লিপিতে[সম্পাদনা | উৎস সম্পাদনা]
دفا ۱: تمام انسان/مرد اجادبھابے برابر اُکر/کراموت/یہاتیرام/تعجو/ انتیبہ ارحق لوئے پویدا ہوی۔ تاي سوباري اےکے اپورےر مطابق بیرادری/ اخوانی اخلاقےر ساتھے رونا/سلوک کرا چای۔
আধ্বব[সম্পাদনা | উৎস সম্পাদনা]
/d̪ɔfa æk | t̪amam insan/mɔrd̪ aɟad̪bʱabe bɔrabɔr okar/karamɔt̪/iɦot̪iram/t̪auɟu/inot̪ibaɦ ar ɦɔk loe̯ pɔe̯d̪a ɦɔe̯ | t̪ad̪er domir o akɔl acʰe | t̪o ʃɔbari æke ɔporer mot̪abek berad̪ori/ikʰo̯ani akʰlaker ʃat̪ʰe ro̯a/ʃuluk kɔra cai /
মধুসূদন দত্তের বঙ্গভাষা কবিতা[সম্পাদনা | উৎস সম্পাদনা]
বাংলা লিপিতে[সম্পাদনা | উৎস সম্পাদনা]
<poem>হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন;— তা সবে, (অবোধ আমি!) অবহেলা করি, পর‐ধন‐লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।</poem>
শাহমুখী লিপিতে[সম্পাদনা | উৎস সম্পাদনা]
<poem>ہے بنْگو بھنڈارے تنو بیبیدھو رتن تا شے ، ( ابودھ آمی ) ابوہےلا کری
پرودهن لوبھے متّ، کرینو بهْرمݨ پرودیشے
، بھِکّھا بْرتّی کو کّھݨے آچری</poem>
আরও দেখুন[সম্পাদনা | উৎস সম্পাদনা]
- ইসলামীকরণ
- আরবিকরণ
- বাংলার রোমানীকরণ
- সংস্কৃতায়ন (হিন্দুধর্ম)
- রোমান উর্দু
- আরবির রোমানীকরণ
- দেবনাগরী প্রতিবর্ণীকরণ
- মাল্টীয় ভাষা - প্রাচীন আরবি ভাষার একটি রোমানীকৃত ভাষা রূপ
- ফিজি হিন্দি - হিন্দি ভাষার একটি রোমানীকৃত ভাষা রূপ
- বাংলা ভাষা আন্দোলন
- আরবিকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব
- ইসলামে আরবি ভাষা
- পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি
তথ্যসূত্র[সম্পাদনা | উৎস সম্পাদনা]
- ↑ টেমপ্লেট:Cite news
- ↑ টেমপ্লেট:Cite news
- ↑ ৩.০ ৩.১ টেমপ্লেট:বই উদ্ধৃতি
- ↑ টেমপ্লেট:Cite book
- ↑ টেমপ্লেট:বই উদ্ধৃতি
- ↑ টেমপ্লেট:বই উদ্ধৃতি
- ↑ স্ক্রিপ্ট ত্রুটি: "উদ্ধৃতি" নামক কোনো মডিউল নেই।
- ↑ আহমদ ছফা মহাফেজখানা, প্রথম খণ্ড, বেহাত বিপ্লব ১৯৭১ - সলিমুল্লাহ খান সম্পাদিত (অন্বেষা প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ২০০৭), পৃষ্ঠা ১০৮
- ↑ স্ক্রিপ্ট ত্রুটি: "উদ্ধৃতি" নামক কোনো মডিউল নেই।
- ↑ টেমপ্লেট:Cite book
- ↑ টেমপ্লেট:Cite book
- ↑ টেমপ্লেট:Cite web
- ↑ টেমপ্লেট:Cite book
- ↑ টেমপ্লেট:Cite book
- ↑ টেমপ্লেট:Cite book
- ↑ টেমপ্লেট:Cite book
- ↑ টেমপ্লেট:বই উদ্ধৃতি
- ↑ টেমপ্লেট:বই উদ্ধৃতি
- ↑ ১৯.০ ১৯.১ টেমপ্লেট:Cite book
- ↑ টেমপ্লেট:বই উদ্ধৃতি
- ↑ টেমপ্লেট:বই উদ্ধৃতি
- ↑ টেমপ্লেট:Cite book
- ↑ টেমপ্লেট:বই উদ্ধৃতি
- ↑ টেমপ্লেট:Cite book
- ↑ টেমপ্লেট:বই উদ্ধৃতি
- ↑ টেমপ্লেট:বই উদ্ধৃতি
- ↑ স্ক্রিপ্ট ত্রুটি: "উদ্ধৃতি" নামক কোনো মডিউল নেই।
- ↑ স্ক্রিপ্ট ত্রুটি: "উদ্ধৃতি" নামক কোনো মডিউল নেই।
- ↑ স্ক্রিপ্ট ত্রুটি: "উদ্ধৃতি" নামক কোনো মডিউল নেই।
- ↑ স্ক্রিপ্ট ত্রুটি: "উদ্ধৃতি" নামক কোনো মডিউল নেই।
- ↑ স্ক্রিপ্ট ত্রুটি: "উদ্ধৃতি" নামক কোনো মডিউল নেই।
- ↑ টেমপ্লেট:বই উদ্ধৃতি
- ↑ টেমপ্লেট:Cite book
- ↑ টেমপ্লেট:Cite book
- ↑ https://dsal.uchicago.edu/dictionaries/bhattacharya/frontmatter/frontmatter.pdf