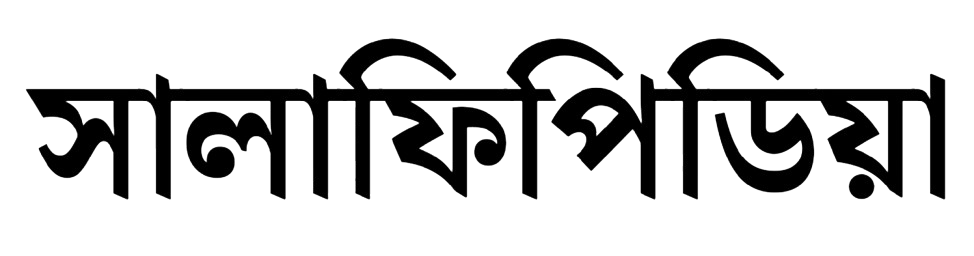ফুসুলুন ফী আদিয়ানিল হিন্দ
স্ক্রিপ্ট ত্রুটি: "Infobox" নামক কোনো মডিউল নেই।{{#switch:
{{#if:
| {{{demospace}}}
| {{#ifeq:|
| main
| other
}}
}}
| main = {{#if:দারুল বুখারী
মাকতাবুর রুশদ |}}{{#if: |}}{{#if: |}}{{#if: |}}{{#if: |}}{{#if: |}}
| other
| #default =
}}
টেমপ্লেট:ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম
ফুসুলুন ফি আদিয়ানিল হিন্দ, আল-হিনদুসিয়াতু, ওয়াল বুজিয়াতু, ওয়াল জাইনিয়াতু, ওয়াস সিখিয়াতু ও আলাকাতুত তাসাওউফি বিহা (فصول في أديان الهند الهندوسية والبوذية والجينية والسيخية وعلاقة التصوف بها, হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ ধর্ম তথা ভারতীয় ধর্মসমূহের সমীক্ষা ও সুফিবাদের সঙ্গে এসবের সম্পর্ক') হলো জিয়াউর রহমান আজমী কর্তৃক ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে হিন্দুধর্মের উপর লিখিত একটি বই।[১] বইটি ১৯৯৭ সালে দারুল বুখারী, মদীনা মুনাওয়ারা থেকে ও পরবর্তীতে ২০০২ সালে সৌদি আরবের মাকতাবুর রুশদ হতে প্রকাশিত হয়।[২] বইটি ইসলামী অধ্যয়নের অঙ্গনে হিন্দুধর্ম ও ভারতীয় ধর্ম বিষয়ক প্রধানতম গ্রন্থগুলোর মধ্যে অন্যতম। এই বইটিতে ভারতের প্রধান চারটি ধর্ম, হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন এবং শিখ ধর্মকে নিয়ে ইসলামী দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী বৈজ্ঞানিক গবেষণা করা হয়েছে। বইটিতে লেখক দাবি করেন, এই তিনটি ধর্মের মধ্যে মিল রয়েছে এবং তাদের ভিত্তিগুলি বেশিরভাগই প্রাচীন বিশ্বাস, ধারণা এবং রীতিনীতির উপর ভিত্তি করে।
ইতিহাস[সম্পাদনা | উৎস সম্পাদনা]
বইটির লেখক জিয়াউর রহমান আযমি ১৯৪৩ সালে আজমগড়ে বঙ্কে লাল নামে একটি হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৯ সালে, প্রথমে তিনি কুরআন এর একটি সংস্কৃত অনুবাদ খুঁজে পান এবং এটি পড়ে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হন। কয়েকদিন পরে, হাকিম মুহাম্মদ আইয়ুব নদভী, যিনি জামায়াত-ই-ইসলামী হিন্দ এর সদস্য ছিলেন, তাকে আবুল আলা মওদুদীর "সত্য ধর্ম" নামে একটি পুস্তিকা উপহার দেন এবং বইটি পড়ে তিনি ইসলামের প্রতি আরও আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং জামায়াত-ই-ইসলামী হিন্দ-এর ইসলামী সেমিনারে যোগ দিতে শুরু করেন। ১৫ বছর বয়সের দিকে ১৯৬০ সালে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি একটি স্থানীয় স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন এবং তারপর আজমগড়ের শিবলি ন্যাশনাল কলেজে ভর্তি হন। তিনি ওমেরাবাদের জামিয়া দারুসসালামে দরসে নিজামি অধ্যয়ন শুরু করেন এবং মদিনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় এবং উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যথাক্রমে ইসলামিক স্টাডিজে বি.এ. এবং এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন। এই বইটি আসলে লেখকের নিবন্ধসমূহের একটি সংগ্রহ, যা মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের "মাগজালাত আল জামিয়াত আল-ইসলামিয়া বিল মদিনাহ আল মুনাওয়ারা (মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ম্যাগাজিন)"-এ প্রকাশিত হয়েছিল[৩] এবং এরপর যখন তিনি মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত হন, তখন তিনি "আদিয়ান আল-আলাম (বৈশ্বিক ধর্মসমূহ)" শিক্ষাদানের দায়িত্বও পালন করেন। অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি যখন তার উপর এ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়, তিনি নিবন্ধগুলি থেকে "ধর্ম" এর পাঠ প্রস্তুত করেন এবং তারপরে এই নিবন্ধগুলিকে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য পুনর্বিন্যাস করে বই আকারে প্রকাশ করেন।[৩][৪] এখন এই দুটি বই "ধর্ম" নিয়ে কাজ করে, যথা "ইহুদিবাদ এবং খ্রিস্টধর্মে অধ্যয়ন" (دراسات في الیهودیة والنصرانیة) এবং "ভারতের ধর্মসমূহের সমীক্ষা", একত্রে এক খণ্ডে "দিরাসাত ফিল ইয়াহুদিয়াত ওয়াল মাসিহিয়াত ওয়াল আদিয়ানিল হিন্দ" (دراسات في اليهودية و المسيحية و أديان الهند, ইহুদি, খ্রিস্টান এবং ভারতীয় ধর্মে অধ্যয়ন) নামে প্রকাশিত হয়েছে, যার ৭৮৪ পৃষ্ঠা রয়েছে,[৩] বিষয়বস্তুর মিলের কারণে এটি সৌদি আরবের বিখ্যাত মুদ্রণালয় মাকতাবাত আল-রুশদ দ্বারা প্রকাশ করা হচ্ছে[৩] এবং এ পর্যন্ত এর সাতটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।[৫] স্থানীয় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের কাছে খুবই জনপ্রিয় হওয়ায় এই প্রতিষ্ঠানটি প্রতি বছর এই বইটি প্রকাশ করছে।[৬][৩]
বিষয়বস্তু[সম্পাদনা | উৎস সম্পাদনা]
হিন্দুধর্ম[সম্পাদনা | উৎস সম্পাদনা]
আজমী গ্রন্থটিতে হিন্দুধর্ম সম্পর্কে বলেন, ভারতে মহেঞ্জোদারোতে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে (কৃষ্ণাঙ্গ হামীয়) কোল জাতি বাস করতো, (শ্বেতাঙ্গ ইয়াফেসীয়) তুরানিরা এসে তাদের পরাভূত করে তাদের সাথে মিশ্রিত হলে দ্রাবিড় জাতির উদ্ভব হয়, যারা সিন্ধুতে মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা শহরে নিবাস তৈরি করে এবং এরপর তা থেকে দক্ষিণ ভারতে ছড়িয়ে পড়ে, এবং তারা তাদের ভাষা অনুযায়ী কন্নড় মালয়ে তামিল ও তেলেগু এই চারটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে।[৩] এ সময় কয়েক শতক ধরে তারা সিন্ধুনদের পূর্বদিক থেকে আসা (ইয়াফেসীয়) আর্যদের সাথে সংঘর্ষ চালিয়ে যায়, এবং এই সিন্ধু শব্দ অনুসারে গ্রিক ও ইরানিরা হিন্দু নামটি প্রদান করে।[৩] একপর্যায়ে আর্যরা বিজয় লাভ করলে দ্রাবিড়সহ স্থানীয় অধিবাসীরা তাদের আনুগত্য গ্রহণ করে এরপর আর্যরা সমাজ ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো শুরু করে এবং ভারতবর্ষের অধিবাসীরা বৈদিক সমাজে প্রবেশ করে। আজমি প্রত্নতাত্ত্বিক সাদৃশ্যের পাশাপাশি সংস্কৃত ও ফার্সি ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক মিলের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, আর্যরা ইউরোপিয়ান তথা পারস্য বংশোদ্ভূত ছিল এবং তিনি ভাষাবিজ্ঞানের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, সংস্কৃত ভাষাভাষী আর্য ও ফারসি ভাষাভাষীরা একই ভূখণ্ডের বাসিন্দা ছিল, এবং তারা পারস্য থেকে এসেছিল।[৩] এরপর আর্যরা ভারতের স্থানীয় অধিবাসীদের মর্যাদার ক্রমানুসারে চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে, এগুলো হলো ব্রাহ্মণ (আর্য পুরোহিত বা ধর্মগুরু), ক্ষত্রিয় (রাজপুত যোদ্ধা বা মারাঠা), বৈশ্য (তুরানি দ্রাবিড় ব্যাপারী বা ব্যবসায়ী ও কৃষক) ও শূদ্র (তুরানি দ্রাবিড় মজদুর বা শ্রমিক), যার প্রথম দুটি ছিল আর্য উচু শ্রেণী ও শেষ দুটি ছিল দ্রাবিড় নিচু শ্রেণী। আজমির মতে, এদের মধ্যে শূদ্ররা আর্যদের কাছে প্রবল নির্যাতন ও অসম্মানের পাত্র হওয়ার ফলে বিংশ শতাব্দীর দিকে তারা ব্যাপকহারে ধর্মান্তরিত হয় এবং একটি বড় সংখ্যার জনগোষ্ঠী ইসলাম গ্রহণ করে, বিশেষ করে তামিলনাড়ুসহ বিভিন্ন স্থানের দলিত সম্প্রদায়, যাদের ইসলাম ধর্মে স্বেচ্ছায় ধর্মান্তরের বিষয়ে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম হতে প্রাপ্ত বাবাসাহেব আম্বেদকরের উদ্ধৃতিসহ বহুসংখ্যক তথ্যসূত্র আজমি উল্লেখ করেন।[৩] এরপর হিন্দুগণ গ্রন্থ রচনা মনোনিবেশ করে যা পাঁচটি যুগে বিভক্ত ছিল। যথাক্রমেঃ[৭]
- প্রথম যুগে চারটি বেদ রচনা করা হয়। আজমি বলেন, বৈদিক সংস্কৃতি ছিল আর্য ও স্থানীয় দ্রাবিড়ীয় সংস্কৃতির মিশ্রণের ফসল। এছাড়া বেদকে আব্রাহামিক সহিফা পুস্তিকা দাবি করার প্রচলিত ধারণাকে তিনি নিজস্ব যুক্তিতে নাকচ করেন।[৩]
- দ্বিতীয় যুগে হিন্দু দার্শনিকগণ উপনিষদ রচনা করেন, উপনিষদসমূহে সুফিবাদ তথা তাসাউফের প্রাথমিক ধারণাগুলো সন্নিবেশ করা হয়, যার সাথে সম্পৃক্ত ছিল মনসুর হাল্লাজ, ইবনে আরাবী ও সারমাদ কাশানি, যারা নির্বাণ[৩] ও ওমের সাথে মিলিয়ে ওয়াহদাতুল ওজুদ রচনা করে,[৩] এছাড়াও ইবনে হাবিত, আহমদ ইবনে নামুস, আবু মুসলিম খোরাসানি ও মুহাম্মদ ইবনে জাকারিয়া রাজি হিন্দুধর্মে বর্ণিত পুনর্জন্মের ধারণা ইসলামের নামে প্রচার করেন।[৩] এছাড়াও এ সময় ভারতের সম্রাট জালাল উদ্দিন আকবরের শাসনামলে আল্লাহ উপনিষদ নামে একটি উপনিষদ রচনা করা হয়, যেখানে ইসলামে স্রষ্টার ধারণা নিয়ে আলোচনা করা হয়।
- তৃতীয় যুগে ধর্মীয় রীতিনীতির সংকলন প্রস্তুত করা হয়। এসময় স্মৃতি গ্রন্থসমূহ লেখা হয়, যার মধ্যে মনুস্মৃতি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।
- চতুর্থ যুগে ভারতবর্ষের অধিবাসীদের সঙ্গে আর্যদের সংমিশ্রণের ফলে আর্য দেবতারা হারিয়ে যেতে থাকে। আর্যরা ইন্দ্রকে বজ্রের দেবতা, অগ্নিকে আগুনের দেবতা, অরুণকে আকাশের দেবতা এবং ঊষাকে সকালের দেবতা হিসেবে উপাসনা করত। কিন্তু পরে বিষ্ণু প্রতিপালনের দেবতা ও শিব ধ্বংসের দেবতা হিসেবে এসবের স্থান দখল করে এবং এসব দেবতার গুণকীর্তন করে পুরাণ গ্রন্থসমূহ রচনা করা হয়। গ্রন্থগুলোর বিভিন্ন স্থানে সৃষ্টির উপাখ্যান, পুনরুত্থান ও দুই মনুর মধ্যকার কাল তথা সৃষ্টিজগতের দুই ধ্বংসের মধ্যবর্তী সময়ের বিবরণ দেয়া হয়েছে। হিন্দু বিশ্বাস মতে এই মহাবিশ্ব অবিনশ্বর। অসংখ্যবার এর বিনাশ হয়ে আবার তা নতুনভাবে সৃষ্টি হয়। আজমি আরও দাবি করেন, যেহেতু আর্য অভিপ্রয়াণ খ্রিস্টান সাধু পলের সময় মিশর ও সিরিয়ার মধ্য দিয়ে ঘটে, সেকারণে আর্যগণ পরবর্তীতে সাধু পলের তৈরি খ্রিস্টধর্মীয় ত্রিত্ববাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও মহাদেবের (শিবের) সমন্বয়ে ত্রিদেবীয় ঐশ্বরিক ধারণা তৈরি করে।[৩]
- পঞ্চম যুগে যুদ্ধবিগ্রহের বিবরণ সম্বলিত মহাভারত, গীতা ও রামায়ণ রচনা করা হয় যেগুলোতে আর্য নেতাদের যুদ্ধবিগ্রহের আলোচনা এবং যুদ্ধে তাদের অর্জিত বিজয়ের বিবরণ তুলে ধরা হয়।[৭]
এছাড়াও হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহে ইসলামী নবী মুহাম্মাদের আগমনের কথাসহ বিভিন্ন ইসলামী সুসংবাদসমূহের যে বর্ণনা আছে বলে প্রচলিত আছে, যা নিয়ে মুহাম্মদ ইব্রাহিম মীর শিয়ালকোটি ও সানাউল্লাহ অমৃতসরীসহ আরও অনেকে বিংশ শতকের শুরুতে গ্রন্থ রচনা করেন,[৩] সে ব্যাপারে আজমী বলেন, মুসলিমদের সর্বসম্মত মতানুসারে হিন্দু ধর্মগ্রন্থ সমূহ আসমানী কিতাব না হলেও হিন্দুধর্মে বর্ণিত এসকল ইসলাম-সম্পর্কিত ভবিষ্যৎবাণী অন্তর্ভূক্ত হওয়ার ব্যাপারে তিনটি ব্যাখ্যা থাকতে পারে, প্রথমটি হলো,
- আর্যরা নিজেদের আদিভূমি ত্যাগ করার সময় আর্যদের অভিপ্রয়াণের সময়কালটিতে ইরাকে ঈব্রাহিম নবীর ধর্মের আবির্ভাব ঘটে, তার আমলে হয়তো অন্য কোন নবী ভারতে এসেছিল, যার নির্দেশে এই ভবিষ্যৎবাণীগুলো অন্তর্ভূক্ত করা হয়, অথবা তখন আর্যরা এই অঞ্চল পাড়ি দেওয়ার সময় তাওরাত ও ইব্রাহিমের সহিফাসমূহ হতে এসব গ্রহণ করে,[৩]
- অথবা হিন্দুদের অনেকে বলেন, ঋগ্বেদ তাওরাত থেকে অনুলিপি করা হয়,
- আরেকটি মত হল, হিন্দুরা তাদের গ্রন্থ পরিমার্জনের সময়, ইসলামী শাসনামলে মুসলিম শাসকদের সন্তুষ্ট করতে এগুলো প্রবিষ্ট করে, শিবলি কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক সুলতান মুবিনের মতে, এগুলো বানোয়াট ও হিন্দুদের পরবর্তী সংযোজন, মুসলিম শাসণামলে মুসলিম শাসকদের খুশি করার জন্য হিন্দুরা এগুলো অন্তর্ভূক্ত করেছে,[৩] যেমন কল্কি পুরাণ ও ভবিষ্যপুরাণ, যেগুলোতে ইসলামী বিষয়ে অনেক ভবিষ্যৎবাণী আছে, যুক্তি হিসেবে আজমি বলেন, হিন্দুদের অধিকাংশ ধর্মগ্রন্থ খলিফা মামুন বিন আল রশীদের আমলে বায়তুল হিকমাহতে আরবিতে অনূদিত হয়, কিন্তু তখনকার কোন লেখকই তাদের কোন বইতে এ সকল ভবিষ্যৎবাণী সম্পর্কে কোন কিছু উল্লেখ করেন নি। আরও উদাহরণস্বরূপ আল বিরুনি রচিত ভারততত্ত্ব ("তাহক্বীক মা লিলহিন্দ মিন ক্বাকুলাত মায়কুলাত ফী আলিয়াকল আউ মারযুলা", تحقيق ما للهند من مقولة معقولة في العقل أو مرذولة) ও আরও দুইটি হিন্দু ধর্মগ্রন্থের আরবি অনুবাদের ব্যাপারে বলেন, যেগুলোর কোনটিতে এসকল ভবিষ্যৎবাণীর ব্যাপারে কিছু বলা হয় নি।[৩][৭][৮]
শেষোক্ত মতটির ব্যাপারে আজমি তার অধিক সমর্থন দাবি করেন।[৩][৭][৮] এসব বর্ননার ব্যাপারে আজমি হিন্দু পণ্ডিতদের ৫টি অবস্থান বর্ননা করেন:
- তাদের অনেকে বলেন, এসব সুসংবাদ তাদের ধর্মীয় নেতা ও মহামানবদের সঙ্গে সম্পৃক্ত।
- আবার অনেকে এই সুসংবাদের উদ্দিষ্ট ব্যক্তি শেষ যুগে আবির্ভূত হবেন বলে বিশ্বাস করেন।
- অনেকে আবার এসবকে বানোয়াট বলে মনে করেন। যেমন : দয়ানন্দ সরস্বতী ও তার অনুসারীরা।
- কেউ কেউ এসবকে সত্য বলে মনে করেন; কিন্তু তারা ইসলাম গ্রহণ করেননি। যেমন বেদ প্রকাশ উপাধ্যায় ও রমেশ প্রসাদ।
- আবার অনেকে এসবের সত্যতা স্বীকার করে ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা করলেও নিজেদের জীবন বা নেতৃত্ব হারানোর শঙ্কায় তা করেননি। এদের মাঝে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং প্রকাশ্যে এর ঘোষণা দিয়েছিলেন, তাদের বহু বিপদাপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিলো, স্বজাতির মারধর, গালাগালি ও নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিলো। যারা পালাতে পেরেছিলেন, তারা এর থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন; আর যারা তাদের অধীনে ছিলেন, তাদের পরিণতি শোচনীয় হয়েছিল।
- তাদের অনেকে আবার এ ব্যাপারে চুপ থাকার নীতি অবলম্বন করেন। আজমি ভারতে অনেকের কাছে পত্র লিখে এসব বিবরণ পাঠিয়ে হিন্দু গবেষক ও প্রফেসরদের সামনে তা উপস্থাপনের কথা বললে উত্তরে তারা আজমিকে বলেন, সেই প্রফেসরদের সামনে এসব তুলে ধরা হলে তারা এ ব্যাপারে কথা বলতে চাননি।[৭][৮]
আজমী হিন্দুধর্মের ধর্মবিশ্বাস নিয়ে বলেন,
আজমী ইসলাম সম্পর্কে হিন্দুদের নেতিবাচক ধারণার কারণ হিসেবে বলেন,
বাংলা অনুবাদ[সম্পাদনা | উৎস সম্পাদনা]
২০২১ সালে বাংলাদেশের কালান্তর প্রকাশনী "হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ ধর্মের ইতিহাস" নামে বইটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করে, মহিউদ্দিন কাসেমী বইটির অনুবাদ করেন।[৭]
প্রাপ্তি[সম্পাদনা | উৎস সম্পাদনা]
আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া তার হিন্দুসিয়াত ওয়া তাসুর বাদ আল ফিরাক আল ইসলামী বিহা (টেমপ্লেট:Lang-ar) (হিন্দুধর্ম ও তার দ্বারা প্রভাবিত ইসলামী গোত্রসমূহ) নামক বইটি, যা প্রাথমিকভাবে তিনি থিসিস হিসেবে রচনা করেছিলেন, উক্ত রচনার ক্ষেত্রে তিনি তার শিক্ষক জিয়াউর রহমান আজমীর প্রত্যক্ষ সাহায্য গ্রহণ করেন এবং আজমীর "ফুসুলুন ফী আদিয়ানিল হিন্দ" গ্রন্থটিকে অন্যতমভাবে অনুসরণ করেন।
তথ্যসূত্র[সম্পাদনা | উৎস সম্পাদনা]
বহিঃসংযোগ[সম্পাদনা | উৎস সম্পাদনা]
টেমপ্লেট:মুহাম্মাদের চিত্রায়ন
- ↑ টেমপ্লেট:বই উদ্ধৃতি
- ↑ টেমপ্লেট:বই উদ্ধৃতি
- ↑ ৩.০০ ৩.০১ ৩.০২ ৩.০৩ ৩.০৪ ৩.০৫ ৩.০৬ ৩.০৭ ৩.০৮ ৩.০৯ ৩.১০ ৩.১১ ৩.১২ ৩.১৩ ৩.১৪ ৩.১৫ ৩.১৬ ৩.১৭ ৩.১৮ {{#if: | {{{author}}} }} {{#if: https://books.google.com/books?id=zLGztAEACAAJ&q=%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D8%B1+%D8%A8%D8%B9%D8%B6+%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D9%87%D8%A7 | الهندوسية وتأثر بعض الفرق الاسلامية بها }} {{#if: Dār al-Awrāq al-Thaqāfīyah | Dār al-Awrāq al-Thaqāfīyah. }} {{#if: 28 July 2023 | Accessed: 28 July 2023. }} {{#if: | {{{লেখক}}} }} {{#if: | [{{{ইউআরএল}}} {{{শিরোনাম}}}] }} {{#if: | {{{প্রকাশক}}}. }} {{#if: | তারিখ {{{সংগ্রহ-তারিখ}}}. }}
- ↑ টেমপ্লেট:বই উদ্ধৃতি
- ↑ টেমপ্লেট:বই উদ্ধৃতি
- ↑ টেমপ্লেট:বই উদ্ধৃতি
- ↑ ৭.০ ৭.১ ৭.২ ৭.৩ ৭.৪ ৭.৫ উদ্ধৃতি ত্রুটি:
<ref>ট্যাগ বৈধ নয়;Aনামের সূত্রটির জন্য কোন লেখা প্রদান করা হয়নি - ↑ ৮.০ ৮.১ ৮.২ টেমপ্লেট:Cite journal